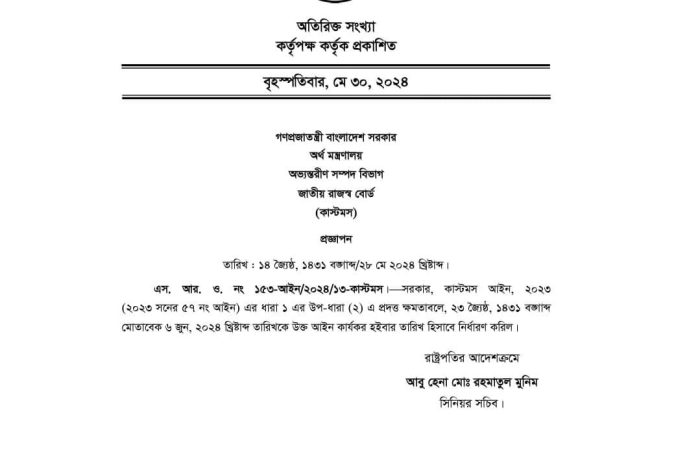আজ ৫ই জুন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘জীববৈচিত্র্য’। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির এ বছরের স্লোগান হচ্ছে ‘ইটস টাইম ফোর নেচার (সময় এখন প্রকৃতির)’।
পরিবেশ বা Environment এতো ব্যাপক একটা শব্দ, যার আওতায় আমাদের পৃথিবীর প্রায় সবকিছুই পড়ে। খুব বড়মাপের স্বার্থবাজ ছাড়া কারো পক্ষে পরিবেশবাদী বা Environmentalist না হয়ে উপায় নেই।
কোন ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে সেটা যে মারাত্মক মহামারীর পরিবেশ তৈরি করতে পারে, এবং সেটা যে নির্বিচারে গাছপালা নষ্ট করে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে ফেলার কারণে হতে পারে, সেটা যারা Contagion (2011) মুভির শেষ দৃশ্যটা দেখেছেন তাদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘুর্ণিঝড় ‘আম্ফান’ ও ‘নিসর্গ’ আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত হওয়া UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) থেকে শুরু করে Kyoto Protocol, 1997 ও Post-Kyoto Negotiations হয়ে Paris Agreement, 2015 পর্যন্ত কোনটাই তেমন সাফল্য পায়নি। তবুও, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটা বৈশ্বিক সচেতনতা তৈরি করা গেছে। Paris Agreement এর মাধ্যমে গৃহীত NDCs (Nationally Determined Contributions) জমা দেয়ার প্রক্রিয়া এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে Global Stocktake গুলোর দিকে পৃথিবীর চোখ থাকবে। এসবের মূল উদ্দেশ্য হলো, বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্রা কে কমিয়ে Pre-industrial Level বা শিল্পায়ন-পূর্ববর্তী মাত্রা থেকে সর্বোচ্চ দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখা। পাশাপাশি সেটাকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমানোর জন্যে চেষ্টা করা। এই দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস ও দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বিস্তর ডিবেট রয়েছে। মোটা দাগে দ্বীপরাষ্ট্রগুলো ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তুলনামূলক কম উঁচু দেশগুলোর জন্যে দেড় ডিগ্রিটাই অত্যধিক আকাঙ্ক্ষিত।
শিল্পায়নে সক্ষমতা ও শিল্পায়নের শুরু থেকেই পরিবেশের ক্ষতি করা, এই দুই কারণের ভিত্তিতে উন্নত দেশগুলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্যে দায়ী করা এবং তদানুসারে তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার যে দাবী তা এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে। বিশ্বরাজনীতির নেতারা কখনো যদি একমত হন, তাহলে এ বিষয়ে আমাদের জন্য কোন অগ্রগতিমূলক আশার বাণী আসতেও পারে। অন্যথায়, আমাদের ভবিষ্যত আমাদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে।
এবারের প্রতিপাদ্য ‘জীববৈচিত্র’ কে রক্ষা করতে হলে বৈশ্বিক উষ্ণতা কে কমানোর কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ১৯৯২ সালে জাতিসংঘে স্বাক্ষরিত হওয়া Convention on Biological Diversity (CBD) এবং পরবর্তীতে Cartagena Protocol ও Nagoya Protocol বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল আন্তর্জাতিক আইনের সমন্বিত রূপরেখা হলো আমাদের জীব-সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যকে টেকসইভাবে ব্যবহার করতে হবে, এসবের সংরক্ষণে আদিবাসী ও স্থানীয় সমাজ কে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে, তাদের ব্যবহৃত কোন জীব-সম্পদ কে কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তাদেরকে ন্যায্য হিসসা দিতে হবে, LMO (Living Modified Organism) / GMO (Genetically Modified Organism) সম্বলিত কোন পণ্যের আমদানি-রপ্তানিতে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করে এমন কোন কিছুর প্রবাহ না ঘটে, ইত্যাদি ইত্যাদি।
মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে Right to Environment কে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার বা Third Generation Right হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।
পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী, ২০১৫ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১৮ক যুক্ত করা হয়েছে, যাতে এসবকিছু আমাদের প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে রক্ষা করা যায়, যেটাকে যথাক্রমে Intragenerational Equity ও Intergenerational Equity বলা হয়। পাশাপাশি, Metro Makers and Developers vs. BELA and Others (2013) মামলায় আমাদের সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ Right to Healthy Environment কে Right to Life এর অন্তর্ভূক্ত বলে রায় দিয়েছিলেন।
এতসব তাত্ত্বিক আলোচনার মূল কথা হলো, প্রত্যেককে যার যার অবস্থান থেকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে। পরিবেশ যেন উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হয়, সে ব্যাপারে সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাতে হবে।
আসুন গাছ লাগাই (অন্ততঃ), পরিবেশ সংরক্ষণ করি। কারণ, “সময় এখন প্রকৃতির”।
মু. আসাদুল্লাহিল গালিব
এলএলবি ও এলএলএম (অধ্যয়নরত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কো-অর্ডিনেটর, টিম সিএলডি